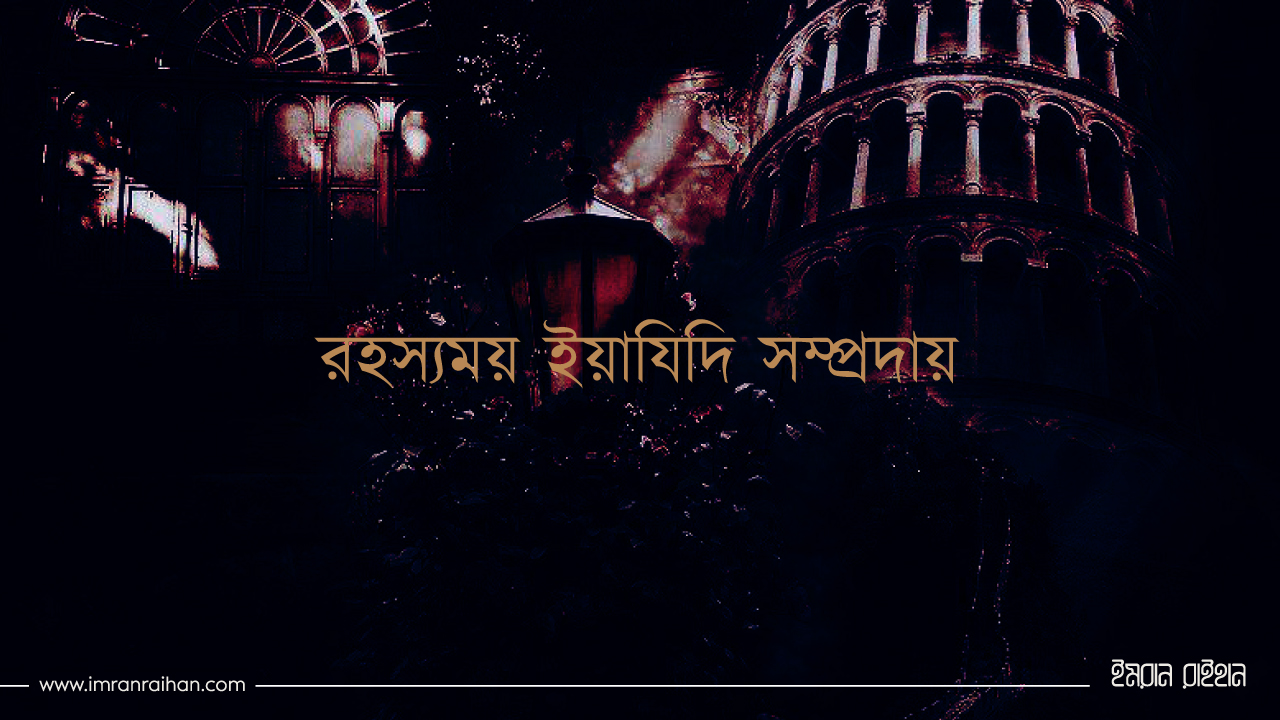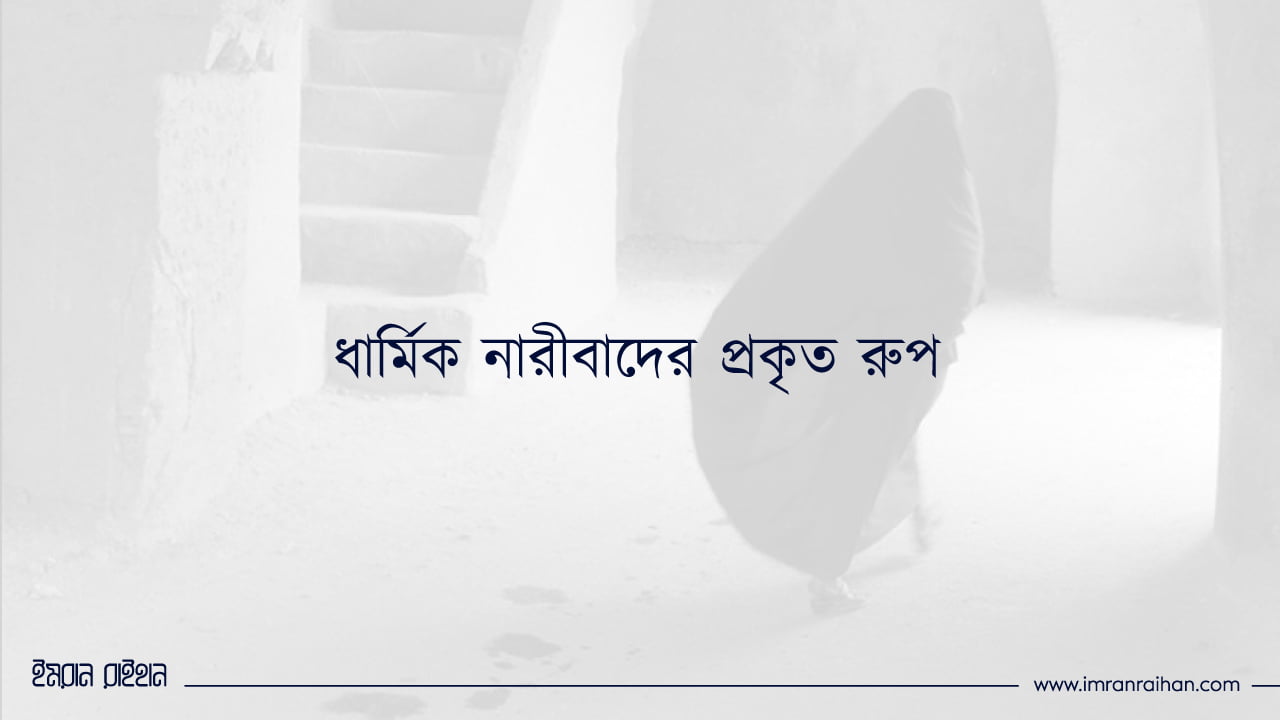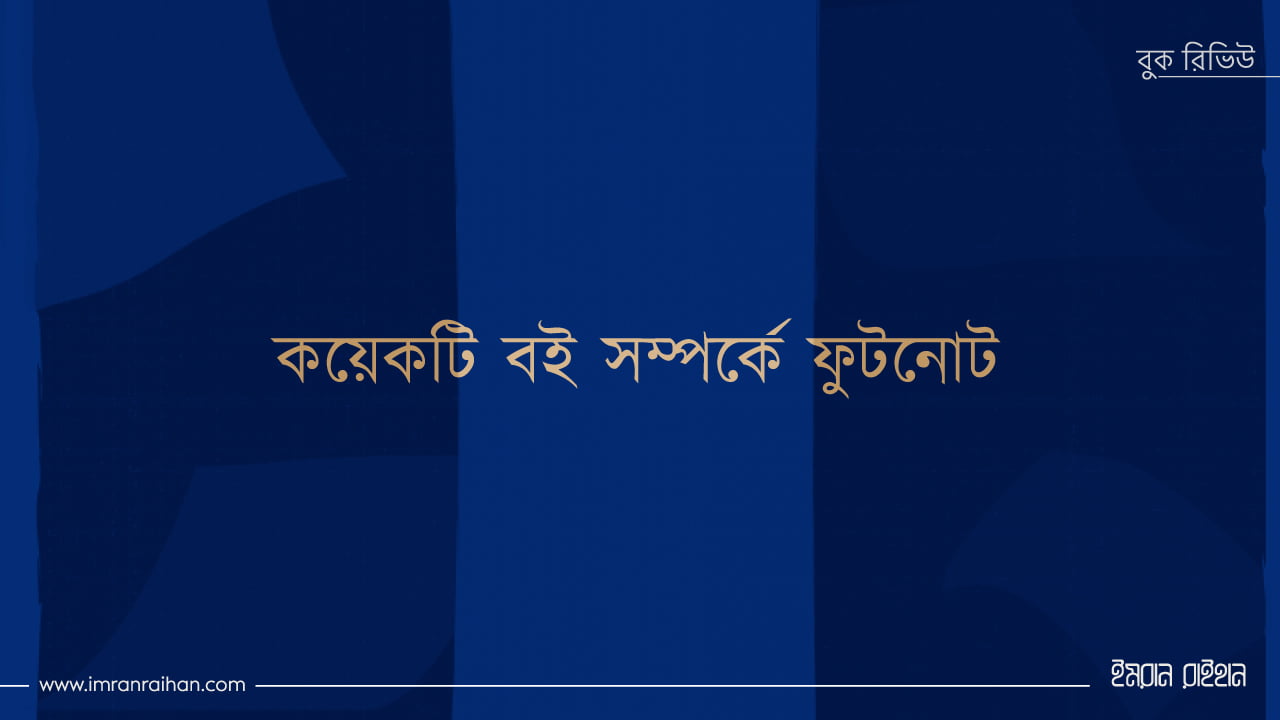হাজার বছর আগে…
মুসলিম পর্যটক ও ভূগোলবিদরা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে। তাদের লেখায় তারা তুলে ধরেছিলেন সেসময়কার মুসলিমদের জীবনযাত্রা ও শহরগুলির বিবরণ। আবু মুহাম্মদ আল হাসান হামদানি, আবুল কাসিম ইবনু হাওকাল, আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু খোরদাদবেহ, মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ শামসুদ্দিন আল মাকদিসি প্রমুখের লেখায় আমরা পাই সে সময়কার এক নিখুঁত বিবরণ।
তারা লিখেছেন, মুসলমানরা তাদের শহরগুলিতে প্রচুর উদ্যান ও নহর নির্মাণ করত। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেত এসব নহর (লেক)। পাশেই থাকতো মনোরম উদ্যান। বিকেল কিংবা অবসরে শহরবাসী ঘুরে বেড়াতো এসব নহরে এবং উদ্যানে। বসরা শহর সম্পর্কে ইবনে হাওকাল লিখেছেন,
‘আমি যখন এ শহরের প্রশংসা শুনতাম, বিশ্বাস করতে মন চাইতো না। কিন্তু যখন নিজের চোখে এ শহর দেখলাম তারপর তা বর্ননা না করে পারছি না। বসরার আবদাসি থেকে আবাদান পর্যন্ত প্রায় দেড়শো মাইলের দূরত্ব। এ পথে কিছুদুর পর পর রয়েছে বিশ্রামাগার। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। লোকেরা এসব বাগানে ঘুরতে আসে। এখানে আছে বড় বড় দিঘী। বারো মাইল লম্বা উবাল্লা নহর এখানেই অবস্থিত। বসরা থেকে উবাল্লা, দীর্ঘ পথের দুধারে রয়েছে মনোরম সব উদ্যান। এগুলো একটা অপরটার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর অবস্থান দেখলে মনে হয় কেউ ফিতা দিয়ে মেপে মেপে সীমানা নির্ধারণ করেছে। পুরো এলাকায় অন্তত এক হাজার নহর রয়েছে এমন, যার ভেতর দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারে। (সুরাতুল আরদ, ১৬০)
তুলনামূলকভাবে ইরাক শুষ্ক এলাকা। এই এলাকাকেই মুসলমানরা এমন গাছগাছালিপূর্ণ বাগান বানিয়ে ফেলেছিল। মুসলিমদের এই প্রবনতা থেকে বাদ পড়েনি কোনও শহরই। ইবনে হাওকাল বোখারা সম্পর্কে লিখেছেন,
‘বুখারার কেল্লার উপর উঠে দাড়াও, তারপর নজর বুলাও চারদিকে। চারদিকে সবুজ, দূরে নেমে এসেছে নীলাভ আসমান। মনে হবে সবুজ কার্পেটের উপর নীল শামিয়ানা টেনে দিয়েছে কেউ। শহরের ঝলমলে মহলগুলোকে মনে হবে আসমানের তারা। সুজলা সুফলা এক শহর। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট ছোট নহর। কোথাও পানির কোনো অভাব নেই। আংগুর, আখরোট, আপেল আর গোলাপের বাগান সর্বত্র। সাগা নদীর দূরত্ব বুখারা থেকে আট দিনের। নদীর দুপাশে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত শস্যভরা মাঠ। এগুলোকে বেষ্টন করে আছে ছোটবড় অসংখ্য নহর। নহরগুলো যেন এসব এলাকার বসতবাড়ি ও বাগানের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। এমন কোনো সড়ক, বাজার ও গ্রাম নেই যেখানে এসব নহরের পানি পৌছাচ্ছে না। প্রতিটি বাড়ির সামনেই শোভা বাড়াচ্ছে পানিভর্তি হাউজ। ফারগানা, শাশ, আশরোসানা ও মাওয়ারাউন্নাহারের সর্বত্র এই একই দৃশ্য। এখানকার পাহাড়ে জন্মে আঙ্গুর, আখরোট, আপেল ও অন্যান্য সুস্বাদু ফল। বাগানে ফুটে গোলাপ, এসব গোলাপ টিকে থাকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত। ফল ও ফুলের মূল্য এখানে সস্তা। যার ইচ্ছা, যত ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। বাঁধা দেয়ার কেউ নেই। পাহাড়ে রয়েছে পেস্তার বাগান। লোকেরা বিনামূল্যেই নিয়ে যায় । (সুরাতুল আরদ, ৩৪৭)
মাওয়ারাউন্নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) তো এমনিতেই সুজলা-সুফলা ভূমি। এখানে মুসলমানদের কাজ সহজ হয়েছিল। অপরদিকে বিষুব রেখার কাছাকাছি অবস্থিত শহরগুলো, সূর্য যেখানে আগুন ঝরায়, মাটি হয়ে উঠে উত্তপ্ত কড়াইয়ের মত, সেখানে মনোরম উদ্যান ও নহর নির্মাণ সহজ ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা শহর নির্মাণ করেছিল শিল্পীর হাত দিয়ে, সবকিছু সাজিয়েছিল নিখুঁত করে। তাদের হাতের ছোঁয়ায় পাথরেও ফুটেছিল ফুল। আল ইদরিসের শাসনামলে আফ্রিকায় আল হাজার নামে একটি বসতি স্থাপন করা হয়। এ শহর সম্পর্কে ইবনে হাওকালের মূল্যায়ন নিম্মরুপ-
‘শহরটি নির্মাণ করা হয়েছে সুউচ্চ এক পাহাড়ের উপর। এখানে চাষ করা হয় জাফরান। পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি টেনে নেয়া হয়েছে শহরের ভেতর। এসব নহর থেকেই জাফরানের বাগানে পানি দেয়া হয়। পশ্চিম আফ্রিকার আরেকটি পাহাড়ি শহর জাবালে নফুসা। পাহাড়ের নিম্মদেশ থেকে এর চূড়ায় উঠতে সময় লাগে তিনদিন। এখানেও রয়েছে নহর ও বাগান। এখানে চাষ করা হয় আঙ্গুর ও ডুমুর। এখানকার যবের রুটি খুবই সুস্বাদু। (সুরাতুল আরদ, ৯২)
মুসলমানদের মধ্যে নহর ও উদ্যান নির্মাণের প্রবনতা কেন জেগে উঠেছিল সে সম্পর্কে মাকদিসীর একটা অনুমান আছে। তার মতে, কোরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যেসব বিবরন এসেছে সেখানে রয়েছে উদ্যান ও নহরের কথা। এ সব বর্ননা থেকে মুসলমানরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ফলে তাদের নির্মিত শহরগুলিতেও তারা উদ্যান ও নহর নির্মাণ করে। (আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, ৪৪৫)
মূলে কারণ যাই হোক, এসব নহরের কারণে মুসলমানদের সেচব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। নিশাপুরের বর্ননা দিতে গিয়ে ইবনে হাওকাল লিখেছেন,
‘এ শহরে ভূগর্ভস্থ নালার মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। এসব নালা নির্মাণ করা হয়েছে শহরবাসীর বাসগৃহের নিচে। শহরের প্রয়োজন শেষ করে পানি চলে যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ও বাগানে। কোথাও কোথাও এসব নালা একশো গজ পর্যন্ত গভীর। এসব নালার সংরক্ষণ ও দেখাশোনার জন্য একজন কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মার্ভ শহরেও দেখেছি, মোরগাব নদী থেকে খাল কেটে আনা হয়েছে। এ খালের পানি নিয়ে আসা হয়েছে শহরের মাঝখানে। সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে পানি বন্টন কেন্দ্র। এখান থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। এখানেও রয়েছে ভূগর্ভস্থ নালা। এসব নালার কোথাও মেরামত করা দরকার হলে শ্রমিকরা তাতে প্রবেশ করে কাজ করে। শীতের দিনে তারা শরিরে মোম মাখিয়ে নেয়, এটা করা হয় সতর্কতা হিসেবে। (সুরাতুল আরদ, ৩১৫)
মুসলিম শাসনামলে জনগনের নিরাপত্তার দিকে প্রশাসকদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে তারা দ্বিধা করতেন না। ইবনে হাওকাল পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম সফর করেছেন। তিনি বেশ নির্মোহভাবে এসব অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, আমার জানামতে আমি মজলিস জমানোর জন্য কোনো মুখরোচক তথ্য দেইনি, কিংবা কোনো এলাকাকে খাটো করার জন্যও কিছু লিখিনি। যা লেখার সংকল্প করেছিলাম ঠিক তা-ই লিখেছি।
ইবনে হাওকাল চোর, ডাকাত ও লুটতরাজের কথা লেখেননি। এ থেকে বোঝা যায় সে সময় (ইবনে হাওকালের মৃত্যু ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে) পর্যন্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। শুধু খোরসানের মরুভূমি সম্পর্কে লিখেছেন, সেখানে কিছু ডাকাতদের আস্তানা ছিল। এর কারণ হলো, সেই অঞ্চলটি নির্দিষ্ট কোনো প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনে ছিল না। উমাইয়া যুগের শুরুর দিকে এন্টিয়ক ও লাসিসার মধ্যবর্তী স্থানে বাঘের সংখ্যা বেড়ে যায়। পথচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকে। এ সংবাদ শুনে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক আদেশ দেন দ্রুত এসব বাঘকে হত্যা করতে। ঐতিহাসিক আবু মুহাম্মদ আল হাসান হামদানি লিখেছেন, খলিফার আদেশ পেয়ে বাঘ হত্যার প্রস্তুতি নেয়া হয়। রাস্তার মাঝে গর্ত করে মহিষ রেখে দেয়া হয়। বাঘ এসব মহিষকে আক্রমন করে গর্তে পড়ে যায়। ফাঁদে বন্দি হয়। এভাবে প্রচুর বাঘ ধরা হয়। এ কাজে টোপ হিসেবে প্রায় চার হাজার মহিষ লেগেছিল।
দজলা নদীর একটি মোহনা মিলিত হয়েছিল উবাল্লা নহরের সাথে। মিলনস্থলটি ছিল গভীর। সবসময় পানি ফুঁসতে থাকতো সেখানে। বেশিরভাগ জাহাজ ও নৌকা এই ঘূর্ণিপাকে আটকে যেত। ডুবে যেত। এই নৌপথটি ছিল খুবই বিপদজনক। কিন্তু এই পথ ব্যবহারে দূরত্ব কমে যেত। ফলে এই পথটি নিরাপদ করাও দরকার ছিল। আর একাজে এগিয়ে এলেন একজন মুসলিম নারী। হ্যা, ঠিক শুনছেন একজন মুসলিম নারী। এই নারী হলেন, আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী যুবাইদা খাতুন। তিনি আদেশ দেন পাথর নিক্ষেপ করে এই স্থানের গভীরতা কমিয়ে ফেলতে। তাই করা হয়। দিনের পর দিন এই স্থানে পাথর ফেলা হয়। ফলে গভীরতা কমে যায়। পানির ঘূর্ণিপাকও চলে যায়। (সুরাতুল আরদ, ১৬০)
নিরাপত্তা চৌকি ছিল সর্বত্র। সাথে ছিল মুসলিম সেনাছাউনি। বিজয়ী বেশে মুসলিমরা যে এলাকায় গিয়ে থামতো তাঁকে বলা হত সাগুর। আর শত্রুদের দিকে মুখ করে যে সেনাছাউনি নির্মাণ করা হত তাঁকে বলা হত রিবাত। নিয়মিত সেনাবাহিনীর বাইরেও সাধারণ জনগন যখন জিহাদে সময় ব্যায়ের ইচ্ছা করত তখন তারা এসব রিবাতের কোন একটিতে চলে যেত। সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, ফলে সাধারণ মানুষ চাইলেই সহজে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারত। এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবরাহিম বিন আদহাম ও অন্যান্য আলেমদের জীবনিতে আমরা দেখি তারা বছরের কয়েক মাস এসব সীমান্ত চৌকিতে অবস্থান করে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।
ইবনে হাওকাল তরতুস শহরের রিবাত ঘুরে দেখেছিলেন। সেখানে তখন এক লাখ সেনা অবস্থান করছিল। তিনি লিখেছেন, রিবাতে অবস্থানকারী মুজাহিদদের সাথে স্থানীয় জনগনের সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। তারা মন খুলে মুজাহিদদের দান করে। নেতৃস্থানীয় ও ধনী ব্যক্তিরা রিবাতের জন্য তাদের সম্পদ ওয়াকফ করেন। সেনা ছাউনিতে ইমারত ও দালানকোঠা নির্মাণ করা হত। ঐতিহাসিক হামদানি সিরিয়ার হারুনিয়া শহরের সীমান্তচৌকিতে এমন অনেক দালান দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, প্রতি পনেরো জন সেনার জন্য এখানে দুটি করে কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। (তারিখে হামদানি, ১৬৪)
মুসলিমরা আবাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সুরুচির পরিচয় দিত। এ সময় তারা আরাম ও রুচি দুটির সমন্বয় করার চেষ্টা করত। ঐতিহাসিক হামদানি লিখেছেন,
‘টিলা বা এ ধরণের উঁচু স্থান হচ্ছে ঘর নির্মাণের জন্য আদর্শ জায়গা। ঘরের দরজা ও খিড়কি নির্মাণের জন্য পূর্ব দিক উত্তম। কারণ, এ ধরণের ঘরে সুর্যের কিরণ সহজেই প্রবেশ করতে পারে, যা সুস্থতার জন্য উপকারি। (তারিখে হামদানি, ১০৩)
সাধারণোত বেশিরভাগ সময়ে মাটির ঘর বানানো হত। এসব ঘরের উপকারিতা হলো, গ্রীষ্মকালে তা উত্তপ্ত হয় না, এবং শীতকালেও মাত্রাতিরিক্ত শীত থেকে এর বাসিন্দাদের নিরাপদ রাখে। ঘর নির্মাণের সময় মেহমানদের কথা চিন্তা করে কিছু প্রশস্ত কক্ষ নির্মাণ করা হত। সে সময় মুসলমানরা মেহমানদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হত। আল্লামা মাকরেজি লিখেছেন,
‘মিসরের মুসলমানদের রীতি হল তারা রান্না করার সময় বেশি করে রান্না করে। যেন মেহমান আসলে তাদের আপ্যায়নে ত্রুটি না হয়। মেহমান না আসলে চাকররা এসব খাদ্য নিয়ে যায়। নিজের পরিবারে বন্টন করে বা বাজারে বিক্রি করে দেয়। (আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খিতাতি ওয়াল আসার, ১/৩১৮)
ইবনে হাওকাল মাওয়ারাউন্নাহারের মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, এখানের বাসিন্দাদের সবাই তাদের গৃহে মেহমানদের জন্য কক্ষ সাজিয়ে রেখেছে। কোনো ভিনদেশী মুসাফির এখানে এলে কে তাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবে এ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। সবাইই আগন্তুককে নিজের মেহমান বানাতে চায়। (সুরাতুল আরদ, ৩৩৮)
ইবনে হাওকাল তেফলেসের মুসলিমদের এক অবিশ্বাস্য ঘটনা লিখেছেন। কোনো এক কারনে তিনি কসম করেছিলেন এই শহরে তিনি কারো মেহমান হবেন না। তার এই কসমের কথা জানতে পেরে শহরের গন্যমান্য ব্যক্তি ও কাজি একত্র হয়ে একটি সভার আয়োজন করে। ইবনে হাওকালও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষ অংশে কাজি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের শহরের নিয়ম হচ্ছে মুসাফির ও তার চাকরবাকর আমাদের ঘরে অবস্থান করবে। এটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা নিয়ম। যদি এটি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। তাহলে আপনাকে দেখে আমাদের জে কষ্ট জাগবে তা থেকে আমরা নিরাপদ থাকবো। আর কসমের ক্ষেত্রে কথা হলো, এর কাফফারা দেয়ার সুযোগ আছে। আমরা সবাই মিলে আপনার কসমের কাফফারা আদায় করে দিতে প্রস্তুত। (সুরাতুল আরদ, ২৪৪)
ভারতবর্ষের মুসলমানরাও এ প্রবনতা থেকে মুক্ত ছিল না। মাওলানা গোলাম আলি আযাদ বিলগ্রামি লিখেছেন, হুসাইন আলি খান যখন আলমগিরের সুবাদার নিযুক্ত হন তখন তার রন্ধনশালায় এত বেশি রান্না করা হত, লোকেরা চাইলেই এক পয়সা দিয়ে বড় এক থালা বিরিয়ানি সংগ্রহ করতে পারত।
এত দূরে যাওয়ার দরকার কী? আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও (শায়খ গিলানি এই লেখা লিখেছিলেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) হায়দারাবাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের রান্নাবান্না যারা দেখেছেন তারা জানেন, অতীতে ধনাঢ্য মুসলিমদের রন্ধনশালা ছিল মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত। এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। যতদিন এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েনি , ততদিন আপনি হায়দারাবাদে বড় বড় হোটেল ও ক্যাফেটেরিয়া দেখেননি।
বলছিলাম, সেকালে মুসলিমরা তাদের ঘর নির্মাণ করত প্রশস্ত করে। ঘরে কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট থাকতো। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ, বাচ্চাদের পড়ার জন্য পৃথক কক্ষ, চাকরবাকরদের থাকার জন্য আলাদা কক্ষ।
মূল- সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী রহ.
রুপান্তর- ইমরান রাইহান